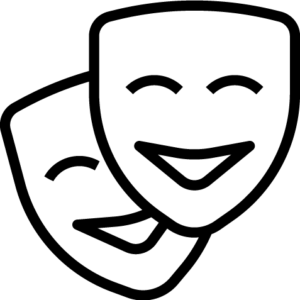১৯১০ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন নাটক রাজা, আগামী বছর এর রচনার শতবর্ষ পূরণ হবে। নিজের কবিতা শত বছর পরে কেউ পড়বে কি না সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন না, যে পাঠক ১৪০০ সালে তাঁর কবিতা পড়ছে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ যেন ঠিক চিনে উঠতে পারেন নি, ‘কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি’, এই প্রশ্নে নতুন যুগের পাঠকের কৌতূহল নিয়ে উৎসাহী হলেও অচেনা পাঠক-বিষয়ে তাঁর সংশয়ও চাপা থকে নি। হালফিল কবিতার সঙ্গে পুরনো কবিতার ফারাক তো অনেক, তারপরও কালজয়ী কবিতার আবেদন কখনও ফুরোবার নয়। তবে সেইসব কবিতার সংখ্যা বেশি নয়, এবং তা এক ধরনের শনাক্তি অর্জন করেছে, আগ্রহীজনেরা সেইসব কবিতা সম্পর্কে জানেন। কিন্তু নাটক, নাটককে তো সবসময়ে সমকালীন হয়ে উঠতে হয়, কোন্ নাটক কখন কীভাবে প্রযোজনার কল্যাণস্পর্শে সমকালীন মাত্রা পাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। নাটক একান্তই বর্তমানের শিল্প, বাস্তব সময়ে বাস্তব মানুষ দ্বারা অভিনীত শিল্প এবং সমকালের দর্শকদের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার সার্থকতা অর্জিত হয়। এই সার্থকতার জন্য নাটককে আবার নতুন করে সজীব হয়ে উঠতে হয়, অতিক্রম করতে হয় পূর্বকালের গণ্ডি। ফলে নাটকের ইন্টারপ্রেটেশন বা ব্যাখ্যা অত্যন্ত জরুরি, নাটক মঞ্চায়নের পেছনে থাকে যে নাট্যদর্শন তথা জীবনদর্শন সেটা যে-কোনো পুরনো নাটককে সমকালের জন্য তাৎপর্যময় করে তুলতে পারে, আর শত বছর আগের নাটক তো সেই বিবেচনাতে কখনো প্রাচীন হয়ে পড়ে নি, যেমন মনে হতে পারে শত বছর আগের কবিতাকে, সে-ক্ষেত্রে পুরনো নাটক কেবল অপেক্ষায় থাকে নতুন সৃজনস্পর্শের।
এই পটভূমিকাতে যখন জানা গেল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে প্রাচ্যনাট মঞ্চে আনছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজা তখন নড়েচড়ে বসতে হয়েছে, কেননা প্রাচ্যনাট এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণের সৃজনউৎসাহের পরিচয় বহন করে, বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে প্রথাগত ভাবনার সীমানা প্রসারিত করবার তাগিদ তারা বারবার মেলে ধরেছে, সেই সার্কাস, সার্কাস প্রযোজনা থেকে দলটি দুঃসাহসী হিসেবে নাট্যজনের স্বীকৃতি অর্জন করেছে, যদিও আমরা এও জানি সাহস সবসময়ে শিল্পের সমার্থক হয় না, তবে অভ্যস্ত ভাবনার গণ্ডি ভাঙতে সাহসের কোনো বিকল্পও নেই। কবুল করতে হয় আজাদ আবুল কালামের নির্দেশনায় প্রাচ্যনাট রাজা নাটক মঞ্চে আনছে জেনে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলাম। রাজা রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টির শুরুর দিকের ফসল, মঞ্চে এই নাটক কখনো বিশেষ আনুকূল্য পায় নি, নানা কারণে রাজা নাটকের অভিনয় কষ্টসাধ্য হয়ে রয়েছে। এমনিতে রবীন্দ্রনাথের মঞ্চভাগ্য খুব প্রসন্ন নয়, আর রাজার ক্ষেত্রে তো এটা আরো বেশি করে প্রযোজ্য। রাজা বলা যায় রবীন্দ্রনাথের নবনাট্যচিন্তার অগ্রণী বাহক, এই নাটকের অনেক উপাদান রবীন্দ্রনাটকে পরে বারবার ফিরে এসেছে। আড়ালে যে-রাজা থাকেন তাঁর পূর্ণ মহিমা আমরা দেখতে পাই অনেক পরের রক্তকরবী নাটকে। আবার রাজা নাটকের রূপান্তর তো রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঘটিয়েছেন অরূপরতন এবং শাপমোচন রচনা করে। সৃষ্টিশীলতার এই খেলায় রবীন্দ্রনাথের কোনো বিরাম ছিল না। রাজা নাটকের ঠাকুরদা, যাঁকে প্রথম দেখি দু’বছর আগে রচিত শারদোৎসব-এ, তিনি তো এরপর কতভাবেই না দেখা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাটকে, ডাকঘর, ফাল্গুনী, অচলায়তন, রথের রশি, মুক্তধারা এবং রক্তকরবী-তে। দেখা গেছে এক নাটকের উপাদান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেছেন আরেক নাটকে, একই নাটককে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানাভাবে দেখেছেন, সৃষ্টি নিয়ে এ-যেন এক খেলাই ছিল তাঁর, নাটক বিষয়ক প্রচলিত ধারণার তিনি বিশেষ ধার ধারেন নি, সে-কারণেই বোধ করি বাংলা রঙ্গমঞ্চ তাঁকে নিয়ে কখনও স্বচ্ছন্দ বোধ করে নি।
অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের নাটক নিয়ে এক অচলায়তন বোধ বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। ‘রাবিন্দ্রীক’ বলে রবীন্দ্রনাথের একটি চিরচেনা ভাবমূর্তি অশেষ যতেœ দাঁড় করানো হয়েছে, সেই চেনা রূপের, কিংবা বলা যায় শাস্ত্র নির্দেশিত রূপ-কথার বাইরে কেউ গেলে গেল-গেল রব ওঠে। সেই রবকে দোষ দেয়া থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি, যদি গেল-গেলকে নেতিবাচক না ধরে ইতিবাচক হিসেবে গণ্য করি। গণ্ডির বাইরেই যদি না-যাওয়া যায় তবে তো বলতে হয় দাদাঠাকুরের ফিরে ফিরে আসাতেও বিশেষ কাজ হয় নি, আজও আমাদের থাকতে হবে তাঁর পথ চেয়ে। চির নতুনেরে ডাক দিয়েছিল পঁচিশে বৈশাখ, ফিরে ফিরে চিরচেনাকে পাওয়ার তাগিদ থেকে, সেজন্য চেনা মূর্তিটাকে নিয়ে ভাঙাগড়ার খেলার অধিকার মান্য করে চলতে হবে বৈ কি। আর তাই প্রাচ্যনাট-এর মতো নতুন পথানুসন্ধানী দলের রবীন্দ্রপ্রযোজনায় উৎসাহিত না হয়ে পারা যায় না। সেই প্রত্যাশা তরুণদল কতোটা পূরণ করতে পেরেছে সেটাই বড় বিবেচ্য।
রাজা নাটকের নামপরিচয়ের সঙ্গে প্রাচ্যনাট যোগ করেছে ‘এবং অন্যান্য…’। কেন এই যোগ তা ভালোভাবে বোঝা গেল না। তারা নতুন কিছু যোগ করেছেন নিঃসন্দেহে, এই যোগ অনেকের চোখে পীড়াদায়ক ঠেকবে, কেউ কেউ মারমুখিও হয়ে উঠতে পারেন, সেসব কারণেই কি আত্মপক্ষ সমর্থনের উপায় হিসেবে প্রাচ্যনাট বলতে চাইছে তারা তো কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজা মঞ্চায়ন করছেন না, সেইসাথে রয়েছে নিজস্ব আরো কিছু সংযোজন। প্রশ্ন হলো নতুন বিশ্লেষণ বা সংযোজন ছাড়া কি নাটক মঞ্চস্থ হতে পারে! একশ বছর আগের লেখা নাটক আজকের শিল্পী যখন মঞ্চস্থ করবেন তিনি তো আপন ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেটা করবেন আজকের দর্শকদের জন্য, ফলে যিনি পুরোপুরি ‘রাবিন্দ্রীক’ থাকতে চান তিনিও এর একান্ত নিজস্ব ব্যাখ্যা দাঁড় করাবেন এক কল্পিত রবীন্দ্রসীমানার মধ্যে, যার অন্যথা কোনোভাবে সম্ভব নয়। প্রাচ্যনাট প্রায় যেন ঝড়ো হাওয়ার মতো সৃষ্টিশীল উন্মাদনায় মেতে উঠেছে রাজা নাটক নিয়ে, প্রচলভাঙার সাহসী ব্রত নেয়ার পরও কেন তারা দ্বিধার এমন স্বীকৃতি এঁকে রাখলেন সেটা ঠিক বোঝা গেল না।
দর্শক যখন আসবেন রঙ্গালয়ে তখন থেকে শুরু হয়ে যায় নাটক, বেশ নাটকীয়ভাবে। প্রবেশপথের ওপর লেখা রয়েছে ‘ওয়েলকাম টু স্টেটস’, তারপরে ফয়ার থেকে যখন দর্শক ঢুকবেন নাট্যশালায় তখন দ্বারের ওপর লেখা ‘ইমিগ্রেশন’, জলপাইরঙা পোশাক-পরা সেনাপ্রহরীরা পায়চারি করছে, তারা টিকিট পরীক্ষা করে সবাইকে ঢোকাচ্ছে হলে, দর্শক বেশ হকচকিয়ে যাবেন, পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর রাজা নাটক দেখতে এসে এ-কোন্ রাজ্যে তিনি প্রবেশ করছেন!
এই বিশেষ অবতারণা মনে করিয়ে দিল ষাটের দশকে সোভিয়েত মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ানো মস্কোর তৎকালীন তরুণ-তুর্কি পরিচালক য়ুরি লুবিমভ ও তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত তাগানকা থিয়েটারের কথা। তাগানকার প্রথম সাড়া-জাগানো নাটক ছিল রুশ বিপ্লব-বিষয়ক জন রিডের অবিস্মরণীয় রিপোর্টাজ টেন ডেজ দ্যাট শুক দ্যা ওয়ার্ল্ড, দুনিয়া-কাঁপানো দশ দিন। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকে আগাগোড়া আধুনিক নিরীক্ষার মোড়কে ঢেকে পরিবেশন করেছিলেন লুবিমভ এবং নব-নিরীক্ষায় ভীত সেন্সরপীড়িত সমাজতান্ত্রিক সমাজে তা অভিনব এক নাট্যধারার জন্ম দিয়েছিল। আমি তাগানকা থিয়েটারের এই প্রযোজনা দেখি আশির দশকের শেষের দিকে, ততদিনে লুবিমভ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন; সোলঝেনিৎসিন ও আরো অনেক প্রতিভাবানের মতো একই দুর্ভাগ্য বরণ করেছিল তাঁকে। তো এই নাটকের হলে প্রবেশের আগে দেখা মেলে উর্দি পরিহিত লাল ফৌজের সৈনিকদের, তারা টিকিট হাতে নিয়ে খচ্ করে ঢুকিয়ে দিচ্ছে বেয়োনেটের ফলায়। হলে প্রবেশ করতেই দেখা যায় খোলা ও নিরাভরণ মঞ্চ, এমন কি পেছনের ইট বের করা দেয়ালও দৃশ্যমান, সাইক্লোরামা, পর্দার আড়াল, কোনো কিছুরই বালাই নেই, কেবল মঞ্চের মধ্যভাগে জ্বলছে আগুন আর আটসাঁট লাল পোশাক পরে আগুনের লিকলিকে শিখার মতোই নৃত্যপর রয়েছে এক নারী। হঠাৎ হৈ হৈ করে দর্শকদের ওপর প্রায় যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে একদল সৈনিক, শুরু হয়ে যায় নাটক। রাজা নাটকের সূচনায় আমরা দেখি প্রায় একই ধরনের আবহ, মঞ্চও খোলা, কেবল পেছনের বিশাল দেয়াল জুড়ে কালো ও ধূসরের আঁকিঝুঁকি, অন্ধকারের আবাস, রাজা যেখানে মিলিত হন রানীর সাথে। এর সামনে ক্যাটওয়াকের মতো বাড়ানো রয়েছে মঞ্চ, হালফিল তরুণ-তরুণীদের আরাধ্য-ভূমি। এই খোলা মঞ্চ-এলাকা ঘিরে চলছে সৈনিকদের পায়চারী, ঘণ্টা বাজতে তারা সচকিত হয়ে টান টানভাবে দাঁড়ায়, শুরু হয় নাটক। ক্যাটওয়াকে ফ্যাশনদুরস্ত হাঁটার ছন্দ ছড়িয়ে কুশীলবেরা একে একে দর্শকদের অভিবাদন জানিয়ে যায়, এরপর রাণী সুদর্শনা উচ্চারণ করেন প্রথম সংলাপ, “আলো, আলো কই।” এভাবে শুরু রাজা নাটকের।
আঁধার ঘরে আলোর আকুতি নিয়ে যে-নাটকের যাত্রা, বুঝতে অসুবিধা হয় না এই নাটক প্রতীকের আবরণে মোড়া এবং এর যাত্রা বুঝি অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। প্রাচ্যনাটের উপস্থাপনা থেকে এটাও বুঝে নিতে বিলম্ব হয় না এই নাটক দুই স্তরে অভিনীত হয়ে চলবে, একদিকে রয়েছে পুরাণের পটভূমি, সেখানে এক চিরন্তনতা নিয়ে কাহিনীর উন্মীলন, আরেকদিকে রয়েছে আধুনিক জীবন, ওয়ান-ইলেভেন পরবর্তী বিশ্ব, যেখানে সভ্যতার সংকট ভয়ংকরভাবে মুখ ব্যদান করেছে। রাণী সুদর্শনা, পার্শ্বচর সুরঙ্গমা কিংবা ঠাকুরদা সাবেকী পোশাকে হয়ে আছেন দূরাগত চরিত্র, আর রাজবেশী সুবর্ণ, কাঞ্চীরাজ কিংবা বিদর্ভ, কলিঙ্গ, অবন্তী, পাঞ্চাল, কোশল বা বিরাট রাজ্যের রাজারা যেন আমাদের অতিচেনা হালফিল চরিত্র, বিভিন্ন পরাশক্তির প্রতিভূ, তাদের কারো পোশাকে গোষ্ঠবালকের ছাপ, কৃষ্ণের নয়, টেক্সাসের কাউবয়, কেউ-বা তেলে ভাসমান মধ্যপ্রাচ্যের রাজতন্ত্রের প্রতিভূ, কেউ পূর্বতন রুশি সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রধান, কেউ-বা ক্ষয়িষ্ণু বৃটিশ-সিংহ, এখন আসন পেতে দেয় কাঞ্চীরাজকে, আর কেউ নব্য পরাশক্তির প্রতিনিধি। একটি বক্তৃতামঞ্চের পেছনে দাঁড়িয়ে চলে ক্ষমতাধর রাজনদের বাগাড়ম্বরময় মূক ভাষণ, একেবারে চকিতের দেখা, তারপর পারিষদ এসে তুলে নেয় বক্তৃতার স্ট্যান্ড, ভাঁজ খুলতেই তা হয়ে পড়ে দূরপালার ক্ষেপণাস্ত্র। এর সঙ্গে মিলিয়ে পর্দায় আমরা দেখি জাতিসংঘে রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের ভাষণ, যারা যুদ্ধ বাঁধিয়ে শান্তির কথা বলে যায় অবলীলায়। নাটকে প্রতীককে এমন প্রকাশ্য করে তোলা নিয়ে কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন তবে এটা মেনে নিতে হবে সা¤প্রতিক বিশ্বরাজনীতির পটভূমিকায় রাজা নাটককে বিবেচনা করার মধ্যে কোনো অসঙ্গতি ঠেকে না। নাটক দেখতে দেখতে একসময়ে মনে হবে এই প্রতিস্থাপন মোটেই আরোপিত নয়, বরং বুঝি-বা বর্তমানের প্রেক্ষিত মনে রেখেই একশ’ বছর আগে রচিত হয়েছিল নাটক, আর এ-ক্ষেত্রে পরিচালকের বড়ো অর্জন হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গির এই অভিনবত্ব। রাজা নাটকের এমন এক আধুনিক ব্যাখ্যা যে সম্ভব এবং তা খুব মানানসই, সেটা বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা গেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই নতুন ব্যাখ্যা বলা যেতে পারে ‘রাবিন্দ্রীক’, রবীন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টিকে যেভাবে নব নব রূপে দেখতে চেয়েছিলেন এটা তার এক চমৎকার প্রকাশ। কেবল বলতে হয় রাজা নামপরিচয়ের সঙ্গে ‘এবং অন্যান্য’-এর বাহুল্য যোগ করা প্রয়োজন ছিল না, রাজা নাটক স্বয়ং ধারণ করে এমনি বহুতর ‘অন্যান্য’ ধারণের ক্ষমতা।
প্রসঙ্গত দু-একটি বিষয় উলেখ করা যায়। রাজা নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছিল মূল রচনা প্রকাশের পরপরই এবং রবীন্দ্রনাথ যে-বছর ইংল্যাণ্ডের সুধীমহলে গীতাঞ্জলি পাঠ করে বিদগ্ধজনের মন জয় করেছিলেন, তখন কোনো কোনো অবকাশে তিনি রাজা নাটকটিও পাঠ করে শোনান। রাজা অচিরে কিং অব দা ডার্ক চেম্বার নামে ম্যাকমিলান অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। একটি জার্মান অনুবাদও প্রকাশিত হয় লাইপজিগের কুর্ট ভল্ফ্ প্রকাশনালয় থেকে। প্রকাশনাবর্ষ জার্মান সংস্করণে উলিখিত হয় নি, তবে এর একটি কপি আমার সংগ্রহে রয়েছে, যেখানে দেখা যায় বইটির ক্রেতা মর্গ ফেল্ডম্যানের স্বাক্ষরের সঙ্গে তারিখ রয়েছে ‘ডিসেম্বর ১৯২০’। অনুমান করা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরপর জার্মানিতে প্রকাশিত হয়েছিলে রাজা নাটকের রাজসিক এই সংস্করণ, দামি মোটা কাগজে বড় বড় হরফে মুদ্রিত এই জার্মান সংস্করণের পৃষ্ঠাসংখ্যা ২৪০, সংগ্রহে রাখার মতো সযতœ-মুদ্রিত একটি বই বটে। জার্মান লেখিকা মনিকা কার্ব তাঁর ঠাকুমার বইয়ের আলমারিতে বাল্যকালে এই বই দেখেছিলেন এবং পরে পারিবারিক সূত্রে সেই আলমারি ও বইয়ের মালিকানা তাঁর ওপর বর্তায়। ১৯৯৮ সালে জার্মানিতে স্বল্পকালের পরিচয়ের পর তাঁর বাড়িতে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান এবং পরে আমার হাতে তুলে দিলেন এই সংস্করণ, কোথাকার জল কোথায় গড়ায় সেই আপ্তবাক্যের প্রমাণস্বরূপ যেন, তবে আমার জন্য এ-এক বড় পাওয়া। প্রশ্ন জাগে, প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলায় বিধ্বস্ত জার্মানি রাজা নাটকে কোনোভাবে কি দেখতে পেয়েছিল আপন যুদ্ধ-বাস্তবতার প্রতিরূপ?
রাজা নাটকের জার্মান সংস্করণ প্রকাশের প্রায় একই সময়ে ইউরোপের যুদ্ধের পটভূমিকায় ১৯১৯ সালের দিকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, “রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন অরূপ রাজাকে দেখতে চাইলে; রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় দিলে মালা; তার পরে সেই ভুলের মধ্য দিয়ে পাপের মধ্য দিয়ে, যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোর আপত্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌঁছিয়ে দিলে। প্রলয়ের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির পথ।” এরপর আরো পরিষ্কার করে লিখলেন, “যুরোপের সুদর্শনা যে মেকি রাজা সুবর্ণের রূপ দেখে তাকেই আপন স্বামী বলে ভুল করেছিলÑ তাই তো হঠাৎ আগুন জ্বলল, তাই তো সাত রাজার লড়াই বেধে গেল Ñ তাই তো যে ছিল রানী তাকে রথ ছেড়ে, তার সম্পদ ছেড়ে, পথের ধুলোর উপর দিয়ে হেঁটে মিলনের পথে অভিসারে যেতে হচ্ছে।” রাজা নাটককে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে দেন তা’ আমাদের চমকিত করে এবং আমরা বুঝতে পারি এই ‘রাবিন্দ্রীক’ ব্যাখ্যারই স¤প্রসারণ করেছে প্রাচ্যনাট্য পরাশক্তির যোগসাজসে সৃষ্ট বিভিন্ন আঞ্চলিক সংঘাত ও যুদ্ধের পটভূমিকায় নাটককে স্থাপন করে।
নাটককে এমনি সমকালীন তাৎপর্য দিতে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করে প্রজেকশনকে নাটকের এক বিশেষ উপাদান করে তুলেছেন পরিচালক। নাটক যেহেতু সূচনা থেকেই সমকাল ও চিরকালকে যুগপৎ বরণ করেছে তাই মাল্টিমিডিয়া বিষয়ে কারো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু সবসময় যে তা সুপ্রযুক্ত হয়েছে তা বলা যাবে না। গোড়াতে যখন মাল্টিমিডিয়ার পর্দায় দেখি নাদুস-নুদুস হামটি-ডামটি দেয়ালের ওপর বসে কাস্তে-হাতুড়ি খচিত লাল পতাকা নাড়ছে বড় বেখাপ্পাভাবে এবং অচিরেই ঘটে তার সমূহ পতন, দেখি বার্লিন দেয়াল ভাঙার দৃশ্য, তখন সা¤প্রতিক বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন অভিঘাত আমাদের ভাবনাকে উস্কে দেয়, মাল্টিমিডিয়া নাটকে যোগ করে ভিন্নতর মাত্রা। কিন্তু এরপর থেকে বিভিন্ন সংবাদচিত্রের প্রজেকশন ক্রমাগত পরিচালকের রাজনৈতিক বিবৃতির সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, নাটকের জন্য হয়ে ওঠে অপ্রয়োজনীয় বোঝা, যেসব ছবি আমরা দেখি তাতে থাকে চড়ামাত্রায় প্রপাগাণ্ডার সুর। মনে হয় মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করতে গিয়ে পরিচালক নিজেই অজান্তে এর মোহজালে বাধা পড়েছেন। অথচ প্রাচ্যনাটের প্রযোজনা বিশেষভাবে বুদ্ধিপ্রভ, এবং এর ছাপ নাটকে নানাভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথমত বলতে হয় নাটকের পাঠ বা টেক্সটে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই একে আধুনিককালের পটভূমিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। এই সম্ভাব্যতা শনাক্তকরণ ও উপস্থাপন আমাদের বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। পোশাক পরিকল্পনাতে রয়েছে একই চিন্তার ছাপ, মেকি রাজা সুবর্ণ যেমন হালফিল সামরিক পোশাকের ওপর চাপিয়েছে ফিনফিনে জড়িদার সাবেকী এক আলখালা, যা ভেতরের আধুনিক সজ্জাকে মোটেই আড়াল করছে না, অর্থাৎ তাঁর উপরিভাগের আড়ম্বর নিচের সমরতন্ত্রতাকে ঢাকতে পারগ হচ্ছে না। কিন্তু বুদ্ধির প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে বিশদ বিবৃতিকরণের প্রলোভন দ্বারা। আর তাই আমরা দেখি যুদ্ধ-বিধ্বস্ত প্রান্তরে কাঞ্চী রাজার হাতে শোভা পায় বাইবেল, এর ভেতরের পাতায় সাঁটা থাকে ডলার এবং রাজা তা আবার উঁচিয়ে চারপাশের দর্শকদের জন্য মেলে ধরেন। এমন সব সরলীকরণের ফলে নাটকের প্রবাহ বারবার বিঘিœত হয়েছে। তবু তো নাটক রবীন্দ্রনাথের, তার সংলাপ, গান এবং অন্তর্গত ভাবসম্পদ একে টেনে নিয়ে যায় গভীরতার দিকে, এনে দেয় ভিন্নতর ব্যঞ্জনা।
এই ব্যঞ্জনার বড় দিক হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা যা গ্রামবাসী ও ঠাকুরদার সংলাপে বারবার ফুটে ওঠে, যার প্রধান অবলম্বন হয়েছেন সেই রাজা, যিনি থাকেন আড়ালে, রানীর সঙ্গে মিলিত হন অন্ধকার ঘরে এবং আড়ালের এই রাজা সর্বজনের অন্তরে ঠাঁই করে রাষ্ট্রের ভিন্নতর রূপ মেলে ধরেছেন। এই রাজা নিজেকে জাহির করেন না, দশের মধ্যে তাকে আলাদা বলে চেনাই যায় না, তাঁর ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। এই ভিন্ন রাজার ভিন্নতর উপলব্ধির চেয়ে প্রাচ্যনাটের প্রযোজনায় বেশি জোর পড়েছে প্রচলিত রাজমূর্তির ওপর, যারা আমাদের বেশ চেনা। এইসব রাজার পীড়নমূলক জাহিরি অবস্থানের প্রসঙ্গ নাটকের প্রচারপত্রেও স্থান পেয়েছে, উদ্ধৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, “আমরা তো জানি দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে চোখে পড়ে রাজা,Ñ নিজেকে খুব কষে না দেখিয়ে সে তো ছাড়ে না,” কিন্তু নাটকের শরীরে রাষ্ট্রবিষয়ক ভিন্নতর রবীন্দ্রচিন্তার যে অবস্থান তার বিশেষ প্রতিফলন আমরা মঞ্চায়নে দেখি না। হতে পারে যে-রাষ্ট্রের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তা ইউটোপিয়া, অন্ধকারের রাজার মতো তা এখনও রয়ে গেছে অধরা ও আড়ালে, কিন্তু সেই অবগুণ্ঠনবতী ভাবনার উদ্ভাসনই তো নাটক। পরাক্রমী রাষ্ট্রশক্তি নাটকে বেশ প্রকাশ্য রূপ পেয়েছে কিন্তু বিপরীত চিন্তার তথা জনসাধারণের রাষ্ট্ররূপের পরিচয়টুকু সংলাপে যতোটা প্রকাশিত হয়েছে, নাটকে তেমনভাবে ফুটে ওঠার অবকাশ পায় নি।
পাশ্চাত্য রাষ্ট্রধারণার কেন্দ্রিকতা ও শক্তিসঞ্চয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নানাভাবে পীড়িত করেছিল। বঙ্গভঙ্গ পর্বের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তিনি এর বিপরীতে প্রাচ্যের সমাজনির্ভর রাষ্ট্রধারণার দিকে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছিলেন। সমাজশক্তি যে আত্মশক্তির পরিচয় মেলে ধরে তার ভিত্তিতে ভিন্নতর এক রাজ্যব্যবস্থা মধ্যযুগে প্রাচ্যে বিকশিত হয়েছিল যেখানে সমাজসংস্থার ভূমিকা ছিল প্রবল। উপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ভারতীয় সমাজসংস্থার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রধারণা এবং আত্মশক্তির গরিমাকে মুছে দিয়ে চলেছে প্রবল দাপটে রাষ্ট্রের শক্তিনির্ভর শাসন। রবীন্দ্রনাথ এই দিকটি নিয়ে পরে প্রবন্ধ রচনা বা বক্তৃতাদান বিশেষ করেন নি, তবে কখনোই এমনি দিকদর্শন বিসর্জন দেননি। জীবন-উপান্তে প্রকাশিত কালান্তর-এর রচনাদি এবং আরো স্পষ্টভাবে ‘সভ্যতার সংকট’ প্রবন্ধে সেই চিন্তার অধিকতর সংহত বিচ্ছুরণ আমরা লক্ষ্য করি। তবে তাঁর সৃষ্টিশীল রচনায় বারবার এই প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, বিশেষভাবে তাঁর নাটকে, কিন্তু এতোটাই পরোক্ষে যে বেশিরভাগ সময় তা রসগ্রহিতার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ যে বারবার অন্তরে-বাহিরের দ্ব›দ্ব ও মিলনের কথা বলেছেন প্রায়শ আমরা তা বহিঃস্থ দ্ব›দ্ব হিসেবে বিবেচনা করেছি। প্রাচ্যনাট্যের রাজা প্রযোজনাও সেই বাইরের দ্ব›দ্ব নিয়ে মেতে থেকেছে বেশি, অন্তরের দায় বিশেষ বিবেচিত হয় নি। রাজা নাটক শুরু হয়েছিল সুদর্শনার আলোর আকুতি দিয়ে, ভুল দেবতার উপাসনার ভ্রান্তিমোচন ঘটিয়ে রানী যখন অন্তর-আলোকে পথের রেখা দেখতে পায়, আলোর পথে আসার জন্য শুনতে পায় রাজার আহŸান, “এসো, এবার আমার সঙ্গে বাইরে চলে এসো,Ñ আলোয়,” তখন নাটকের সমাপ্তি। এভাবে আলোর আকুতি দিয়ে নাটকের শুরু এবং আলোর পথের অভিযাত্রী হওয়ার আহŸান জানিয়ে এর সমাপন অর্থাৎ দূরবর্তী এক পথ-চলবার সাধনার কথা এখানে উচ্চারিত হয়েছে, সরল সমাধান মেলে ধরা হয় নি। নাটকের এই পরিণতিতে সর্বসাধারণের মুক্তির সঙ্গে মিশে গেছে ব্যক্তির মুক্তির অভিযাত্রা, কঠিন পথ পাড়ি দিয়ে যে মুক্তিতীর্থে পৌঁছাতে হয়। সমাজের পথপরিক্রমণ আমরা প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু ব্যক্তির পথযাত্রার যন্ত্রণা ও উদ্ভাসন আমাদের গোচরের বাইরে থেকে যায়। নাটকের এই একপেশে বিশ্লেষণের ফলে রানী সুদর্শনা হয়ে পড়েন রাজা নাটকের সবচেয়ে বিভ্রান্ত চরিত্র, আফসানা মিমির মতো শক্তিমান অভিনেত্রীও সুদর্শনাকে নিয়ে কী করবেন বুঝে উঠতে পারেন না। অথচ সুদর্শনা হচ্ছেন নাটকের এমন এক প্রধান চরিত্র যিনি যাত্রাবিন্দুতে ছিলেন যে-অবস্থানে, সমাপ্তি রেখায় হয়ে ওঠেন তার চেয়ে প্রাজ্ঞ ভিন্নতর এক সত্তা। উপলব্ধির পথ বেয়ে চরিত্রের রূপান্তর তাঁর মধ্যেই সবচেয়ে প্রবল।
পুনরায় বলতে হয় প্রাচ্যনাটের রাজা নাটকের সবচেয়ে তাৎপর্যময় দিক হচ্ছে নাটকের টেক্সট অক্ষুণœ রেখে তার আধুনিকায়ন। এভাবে ক্ল্যাসিকসের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে যে নতুন ভাবনার বাহক করা যায় পুরনো টেক্সটকে সেটা সতেজ, সজীব ও গভীরতাসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। এই দেখার দৃষ্টি কোনো মামুলি বিষয় নয়, যদিও উপস্থাপনকালে মনে হবে খুব সাদামাঠা ব্যাপার, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নাট্যচর্চার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ও নবনিরীক্ষার প্রয়াস। তুলনীয় হিসেবে নয়, তবে দেখার চোখের এই ভিন্নতার আরেক পরিচয় হিসেবে উলেখ করা যায় পিকাসোর এক ভাষ্কর্য, তিনি সেখানে নিজ হাতে নতুন করে কিছুই তৈরি করেননি, কেবল পরিত্যক্ত এক সাইকেলের ভাঙা হ্যান্ডেল দেয়ালে টানিয়ে মাঝখানে সিটবেল্টটা জুড়ে দিয়েছিলেন, তাতেই তৈরি হয়ে গেল বিখ্যাত স্কাল্পচার, এ বুল্স্ হেড। অতিচেনা নাটকের পাঠ অক্ষুণœ রেখে দেখার ভঙ্গি পাল্টে দিয়ে অনেক কিছু অর্জন করেছে প্রাচ্যনাট, মনে হয়েছে তাদের এতোসব সংযোজন তথা ‘এবং অন্যান্য’ আসলে নাটকের খোল পাল্টে দিয়েছে, অন্তঃসারে তা রয়ে গেছে একই সাহিত্যরূপধারী, নলচের কোনো কিছুর বদল হয় নি। এভাবে রূপ বদলে দেয়ার লক্ষ্যে নাটকের সংলাপ উচ্চারণেও আমরা দেখি দুটি সমান্তরাল ধারা। আড়ালের রাজা, রানী সুদর্শনা, পার্শ্বচর সুরঙ্গমা কিংবা রোহিনী অথবা ঠাকুরদা কথা বলেন উচ্চারণ ও প্রক্ষেপণের চিরায়ত রীতি মান্য করে। অপরদিকে কাঞ্চীরাজ কিংবা অন্য রাজন্যবর্গ, গ্রামবাসী, পথিক অথবা নাগরিকদল আধুনিককালের চরিত্র হিসেবে সংলাপ উচ্চারণ করেন একান্ত কথ্যভঙ্গিতে। তাঁদের সংলাপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা ম্যানারিজম, যা চরিত্র সকলকে আরো বেশি সমকালীন মাত্রা জোগায়। রবীন্দ্রনাথের সংলাপের টেক্সট অক্ষুণœ রেখে এর স্থান-কাল একেবারে পাল্টে দেয়ার কাজ এমন দক্ষতার সঙ্গে প্রাচ্যনাট করেছে যে মনে হবে নতুন করে বুঝি রচিত হয়েছে এমন সংলাপ, এতো দেহাতী রূপ তো রবীন্দ্রনাথের সংলাপ হতে পারে না। এমন কি করভোদ্যানে রেকর্ড প্লেয়ারে র্যাপ গান বাজানো দুই প্রজার দেখাও আমরা পাই। মূল পাঠ অক্ষুণœ রেখে তার নতুন ব্যাখ্যা ও স¤প্রসারণের এমনি নানা প্রচেষ্টায় ভরে আছে নাটক, কিন্তু দৃষ্টিকটু ঠেকে যখন দেখি নাটক-উপান্তে যোদ্ধৃবেশে ঠাকুরদার প্রবেশের নির্দেশ দেয়া রয়েছে, অথচ সেই প্রবল নাট্যমুহূর্তে ঠাকুরদার বেশভূষায় আমরা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করি না। কল্পনার যে জনরাষ্ট্র নাটকে বিধৃত হয়েছে, ‘আমরা সবাই রাজা’র সেই দেশে আপাতদৃষ্টিতে অক্ষম ঠাকুরদাই সবচেয়ে সক্ষম বীরের ভূমিকা গ্রহণ করেন, তথাকথিত বড় বড় বীরদের রাখা হয় ঘরে বসিয়ে। এই দৃশ্যে মিলিটারিজমের বিরুদ্ধে নাগরিকের অবস্থান প্রকাশের অনেক সুযোগ ছিল, সেসব তো পরিচালক গ্রহণ করেনই নি, বরং মূল নাটকে যা বিধৃত হয়েছে সেটাও যথাযথভাবে অনুসরণে আগ্রহ দেখান নি। ফলে দৃশ্যের নাটকীয়তা ও তাৎপর্য অনেকাংশে ক্ষুণœ হয়েছে।
তবে রসের যে-সমগ্রতায় নাটক হয়ে ওঠে নাটক সেখানে ঘাটতি তৈরি হয়েছে মূলত অভিনয়-দক্ষতায় অসমতার কারণে। অন্ধকারের যে অদেখা রাজা, তাঁর কণ্ঠ আমরা শুনি, কিন্তু সেই স্বর আমাদের আকুল করে তুলতে পারে না। নেপথ্য কণ্ঠ তো যন্ত্র সহযোগেই ভেসে আসে, হয়তো আরো কিছু যান্ত্রিক সুবিধা যুক্ত হলে অন্তরালের কণ্ঠ হয়ে উঠতে পারতো সহজ হয়েও অনন্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সমমানের ছিলেন না, বাচনিক দুর্বলতা অনেকের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে, ফলে সমতালে বয়ে চলে নি নাটক। ঠাকুরদা চরিত্রটি দুরূহ, গানে-বাচনে-অভিনয়ে-নৃত্যে সমভাবে দক্ষ হয়ে উঠতে হয় শিল্পীকে, সাখাওয়াত হোসেন রিজভী চরিত্রের দাবি অনেকাংশে মেটালেও অর্জন করতে পারেন নি সেই দক্ষ-সমগ্রতা, যেটা নাটকের জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সুদর্শনা কেমন করে দুঃখের পথ বেয়ে পৌঁছলেন সত্যমিলনে অন্তরের সেই রক্তক্ষরা অভিযাত্রা নাটকে রূপ দেয়ার চেষ্টায় বিশেষ ব্রতী ছিলেন না আফসানা মিমি, এভাবে চরিত্রটি হারিয়েছে আপন গভীরতা। সুরঙ্গমার সঙ্গে রানীর যে চাপান-উতোর খেলা চলে রাজার রূপ-মাহাত্ম্য নিয়ে, অন্তরের সত্যরূপ খুঁজে ফেরার তাগিদ থেকে, সেটাও সুদর্শনার পথানুসন্ধানে সহায়ক ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যকার সংলাপে গভীরতর দার্শনিকতার পরিস্ফ‚টন ঘটে উঠতে পারেনি। সুদর্শনার চপলতা যে ক্রমে ক্ষয়ে গিয়ে নিরাভরণ সত্যোপলব্ধিতে পৌঁছবার অভিপ্রায়ী হয় তা ধাপে ধাপে উন্মিলীত হয়েছে নাটকের সংলাপে, এর নাটকীয়তা রাজা নাটকের প্রযোজনায় ছিল অনুপস্থিত, তুলনায় বরং সুরঙ্গমা অনেক বেশি কীর্তিময়ীর মর্যাদা পেয়েছেন। এইসব অপূর্ণতার কারণে রসবিচারে রাজা পূর্ণতায় পৌঁছতে পারে নি, কেমন যেন রয়ে গেল টুকরো ও বিচ্ছিন্ন কাজের ভাব, অনেকটাই বুঝি ঠাকুরদার আলখালার মতো। তবে মঞ্চে সকল পাত্র-পাত্রী ছিলেন স্বচ্ছন্দ, একটি সহজিয়া ছন্দ তাঁরা তৈরি করতে পেরেছিলেন চলনে-বলনে-অভিনয়ে, যা মোচন করেছে অন্য অনেক ঘাটতি। এক ঝাঁক নবীন-নবীনার কাছ থেকে এমন মাত্রার কাজ আদায় করে নিতে পারায় পরিচালককে বিশেষ অভিনন্দন জানাতে হয়।
রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যাত্রাপালার ঐতিহ্য থেকে আহরণ করা এই উপাদান তাঁর নাটকে নিজস্ব এক সত্তা নিয়ে বিকশিত হয়। লক্ষণীয় যে এ-ক্ষেত্রে নতুন গান রবীন্দ্রনাথ বিশেষ রচনা করেন নি, পুরনো গান তিনি পাত্র-পাত্রীর মুখে এমন মানানসইভাবে বসিয়ে দিয়েছেন যে মনে হবে নাটকের জন্যই তা বিশেষভাবে রচিত হয়েছে। প্রাচ্যনাট রাজা নাটকের গান পরিবেশনায় কোনো প্রযুক্তির আশ্রয় নেয় নি, অর্থাৎ রেকর্ড করা মিউজিকের পরিবর্তে তারা লাইভ শো করেছে, যেমনটা বলা যায় হালফিল ভাষা ব্যবহার করে। মঞ্চে বসে শিল্পীরা ধরেছেন গান, বাদকদল যেমন সঙ্গত করেছেন, তেমনি তৈরি করেছেন সঙ্গীত-আবহ। ফলে সঙ্গীতে এসেছে সজীবতা এবং প্রাণ সঞ্চার হয়েছে নাটকে, আবহসঙ্গীতও সুপরিকল্পিত ও প্রাণময় হয়ে উঠতে পেরেছে।
প্রাচ্যনাটের রাজায় কোরিওগ্রাফি হয়েছে বড় উপাদান, নাটকের ওপর আরোপিত রাজনৈতিক স্টেটমেন্ট আবহকে যখন ভারি করে তোলে তখন ঠাকুরদার দলবল গানের সঙ্গে নৃত্যের আনন্দরসে সবাইকে মাতিয়ে তুলে নাটককে চলবার ছন্দ জোগায়। কিন্তু সুরঙ্গমা, নাটকে যিনি যোগ করেন দার্শনিক মাত্রা, রাণীর চরম দুঃসময়ে অন্যদের মতো তাঁকে পরিত্যাগ না করে হতে চায় তাঁর পথের সঙ্গী, সাহস বা শক্তি তাঁর হয়তো নেই; কিন্তু রয়েছে এই উপলব্ধি যে সত্যের পথে নামলে ‘সাহস আপনি আসবে, শক্তিও হবে,’ সেই দ্ব›দ্বপীড়িত সময়ে সুরঙ্গমার কণ্ঠে গীত হয় গান, “আমি তোমার প্রেমে হব সবার কলঙ্কভাগী/আমি সকল দাগে হব দাগী”, তাঁর উপলব্ধি ছিল, “শুচি আসন টেনে টেনে/ বেড়াব না বিধান মেলে।” দুঃখ হয়, এই গভীরতাসম্পন্ন গানের এমন এক দলীয় নৃত্য উপস্থাপনা আমাদের দেখতে হয় যা কোনোভাবেই গানের ভাবপ্রকাশক নয়, বরং ভাবসংহারকই বলা যায়।
তবে এহ বাহ্য, এমন কিছু বিভ্রম সত্তে¡ও প্রাচ্যনাটের রাজা আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে বুদ্ধিপ্রভ নিরীক্ষামূলক প্রযোজনা হিসেবে। সাহসিকতা ও চিন্তাশীলতার মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রাচ্যনাট রাজা নাটককে করে তুলেছে একালের রূপকথা, রবীন্দ্রনাথের নবায়ন, এক স্মরণীয় প্রযোজনা।
মফিদুল হক [[email protected]]: প্রকাশক, প্রাবন্ধিক, নাট্য সমালোচক